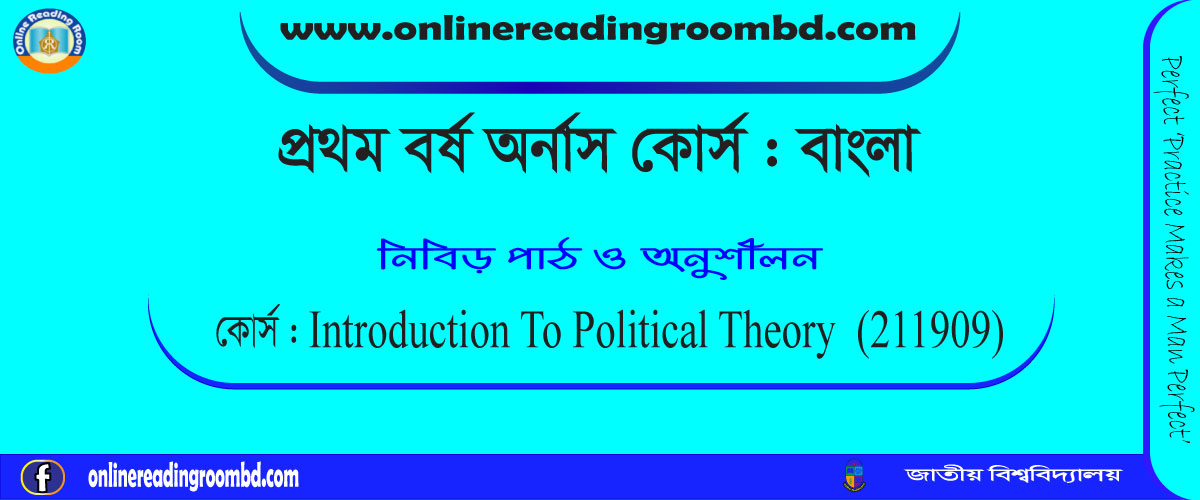
এরিস্টটলের মতে বিপ্লবের কারণ কি? বিপ্লব প্রতিরোধের জন্য তিনি কী কী প্রতিবিধান সুপারিশ করেছেন?
প্রশ্ন: এরিস্টটলের মতে বিপ্লবের কারণ কি? বিপ্লব প্রতিরোধের জন্য তিনি কী কী প্রতিবিধান সুপারিশ করেছেন?
অথবা, এরিস্টটলের মতে বিপ্লবের কারণ কি কি? বিপ্লব প্রশমনের উপায় কী কী ?
উত্তর: ভূমিকা: গ্রিক দর্শন, সভ্যতা ও সংস্কৃতির উজ্জ্বল নক্ষত্র রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জনক এরিস্টটল ছিলেন একজন বাস্তববাদী রাষ্ট্র দার্শনিক। তিনি খ্রিষ্টপূর্ব ৩৮৪ অব্দে থ্রেস প্রদেশের অন্তগর্ত স্ট্যাগিরা নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। এরিস্টটল তার সুপ্রসিদ্ধ ‘ পলিটিক্স’ গ্রন্থের পঞ্চম অধ্যায়ের বিপ্লব সম্পর্কিত মতবাদের ব্যাখ্যা ও বিপ্লবের প্রতিকারের উপায়সমূহ বর্ণনা করেন। তৎকালীন গ্রিসের নগরাষ্ট্রের সরকারের অহরহ পরিবর্তন এবং অভ্যন্তরীণ কোন্দল দার্শনিক এরিস্টটলের চিন্তাধারাকে গভীরভাবে প্রভা্িবত করে। তিনি এরূপ অবস্থা পর্যালোচনা ও পরীক্ষা- নিরীক্ষা করে বিপ্লব সম্পর্কে তার নিজস্ব মতবাদ ব্যক্ত করেন।
ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ সম্বন্ধে জানতে নিচের লিংকে ক্লিক করুন:
বঙ্গবন্ধর ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ -OnlineRedingRoom (onlinereadingroombd.com)
এরিস্টটলের বিপ্লব তত্ত্ব: বিপ্লব একটি ব্যাপকভিত্তিক ধারণা। সাধারণ অর্থে বিপ্লব হলো কোনো ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন। আবার কারো কারো মতে বিপ্লব হলো কোনো ব্যবস্থায় হঠাৎ পরিবর্তন। কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জনক এরিস্টটল বিপ্লব শব্দটি ভিন্ন অর্থে ব্যবহার করেছেন। তার মতে, সংকীর্ণ অর্থে বিপ্লব হলো সাংবিধানিকভাবে স্বৈরতন্ত্রের বা সরকার পরিবর্তন। ব্যাপক অর্থে বিপ্লব হলো গণতন্ত্র, ধনিকতন্ত্র, অভিজাতন্ত্র বা স্বৈরতন্ত্রের যেকোনো পরিবর্তন। সংবিধানের কোনো পরিবর্তন বা নিয়মতান্ত্রিক উপায় একশ্রেণীর শাসক কর্তৃক আরেক শ্রেণীর শাসককে উচ্ছেদপূর্বক ক্ষমতা গ্রহণ। এরিস্টটলের ভাষায়, æRevolution is the changes in constitutions or governments, their nature and number for achieving stability in the political system.”
এরিস্টটলের মতে, বিপ্লবের কারণসমূহঃ এরিস্টটল বিপ্লবের কারণসমূকে দু ভাগে বিভক্ত করেছেন। যথাঃ (ক) সাধারণ কারণ এবং (খ) বিশেষ কারণ।
(ক) সাধারণ কারণ: সাধারণত যে সকল কারণে বিপ্লব সংঘটিত হয় তাকে বিপ্লবের সাধারণ কারণ বলে। নিম্নে বিপ্লবের সাধারণ কারণসমূহ আলোচনা করা হলোঃ
১. মর্যাদার দাবি: গণতন্ত্রে যোগ্যতম ব্যক্তিরা যখন মনে করেন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তিদের ন্যায় তারা রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করতে পারছে না তখন সমঅধিকারের দাবিতে তারা বিপ্লব করে। আবার অভিজাততন্ত্রে এবং ধনিকতন্ত্রে যারা গুণে-মানে শ্রেষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও সাধারণ মানুষের মতো সুযোগ সুবিধা ভোগ করে তখন তারা উচ্চ মর্যাদার জন্য বিপ্লব করে।
২. মুনাফা ও সম্পদ লাভের আশায়: কিছু কিছু উচ্চাভিলাষী বিপ্লব ঘটিয়ে লাভবান হতে চায়। সুচতুর লোকেরা বিপ্লবকে অধিক মুনাফা ও সম্পদ হাসিলের মাধ্যমে হিসেবে ব্যবহার করে। এজন্য তারা বিপ্লবের পথে পা বাড়ায়।
৩. ভীতি বা শাস্তি এড়ানো: অনেক সময় দেখা যায় দেশের বিদ্যমান রাজনৈতিক ব্যবস্থায় কোনো দল বা ব্যক্তি দোষী থাকে এবং শাস্তির ভয়ে ভীত হন, তখন তারা বিপ্লব করে তাদের দোষ এড়াতে চান। এভাবে ভীতির কারণেও বিপ্লব হতে পারে।
৪. সরকারের দুর্নীতি: শাসক গোষ্ঠী যখন নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য যথেচ্ছভাবে সরকারি অর্থ অপচয় করে এবং দুর্নীতি ও অসৎ পন্থায় মুনাফা লাভ করতে থাকে, তখন সেই সরকারের বিরুদ্ধে জনগণ বিপ্লব ঘটানোর জন্য তৎপর থাকেন।
৫. খেতাব প্রদান: সরকার যদি সমশ্রেণীর লোকের মধ্যে বিশেষ কাউকে সম্মানসূচক উপাধি দান করেন তবে যাকে বঞ্চিত করা হলো তিনি নিজস্ব দলের মধ্যে বিপ্লবের ধোয়া ছড়াবেন।
৬. ঘৃণার কারণে: ঘৃণার কারণেও বিপ্লব হতে পারে। কোনো কারণে যদি সরকারের প্রতি জনসমষ্ঠির কোনো এক অংশের মধ্যের ঘৃণার ভাব জাগ্রত হয় তখন বিপ্লব হতে পারে।
৭. জনবিচ্ছিন্ন সরকার: রাষ্ট্রের সরকার যদি জনবিচ্ছন্ন হয় তাহলে জনগণ সরকারকে অপসারণের জন্য বিদ্রোহী হয়ে উঠে। এর ফলে বিপ্লব হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।
৮. বিতর্কিত সিদ্ধান্ত: গুরুত্বপূর্ণ মামলার রায়কে কেন্দ্র করেও কতিপয় শাসনব্যবস্থায় ব্যাপক পরিবর্তনের সূচনা হতে পারে। যেমন, নগরাষ্ট্র হেরাক্লিয়া ও থিবিস এর বিপ্লবাত্মক পরিবর্তনের পিছনে কাজ করেছে আদালতের বিতর্কিত সিদ্ধান্ত।
৯. দল ও উপদলীয় কোন্দল: রাজনৈতিক ক্ষমতার জন্য বিভিন্ন দল উপদলের মধ্যে কোন্দাল শেষ পর্যন্ত বিপ্লবের রূপ নেয়।
১০. বৈষম্যমূলক আচরণ: প্রশাসনিক ক্ষেত্রে যদি সরকার তার বিরোধী পক্ষের সহিত বৈষম্যমূলক আচরণ করেন এবং অহেতুক হয়রানির অপচেষ্টায় লিপ্ত হয় তাহলে রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় এবং বিপ্লবের সূচনা হয়।
এছাড়াও ন্যায় বিচারের অভাব, পদ ও ক্ষমতা, শাসক বর্গের চক্রান্ত এবং ধনী-গরিবের বৈষম্য বৃদ্ধিকেও বিপ্লবের কারণ বলেছেন এরিস্টটল।
(খ) বিশেষ কারণ: বিশেষ বিশেষ গঠনতন্ত্রের যেসব কারণে বিপ্লব বা পরিবর্তন সূচীত হয় এরিস্টটল সেগুলোকে বিপ্লবের বিশেষ কারণ বলে অভিহিত করেছেন। বিপ্লবের বিশেষ কারণসমূহ হলো-গণতন্ত্রের বিপ্লব, অভিজাততন্ত্রেও বিপ্লব, ধনতান্ত্রিক বিপ্লব, রাজতন্ত্রের বিপ্লব, স্বৈরতন্ত্রের বিপ্লব, পলিটিতে বিপ্লব ইত্যাদি।
বিপ্লব প্রতিরোধের/ নিবারণের উপায়: এরিস্টটল তার বিপ্লবতত্ত্বে শুধু বিপ্লবের কারণ উদঘাটন করেই ক্ষান্ত হন নি। সাথে সাথে বিপ্লব নিবারণ বা প্রতিরোধের উপায়সমূহও ব্যাপকভাবে আলোচনা করেছেন, যা নিম্নরূপ:
১. সর্বসম্মত সংবিধান: এরিস্টটলের মতে, বিপ্লব প্রতিরোধের প্রকৃষ্টতম পন্থ হচ্ছে দেশের সংবিধানকে সর্বশ্রেণীর নাগরিকদের সম্মতির উপর প্রতিষ্ঠা করা এবং তা বাস্তবায়নের জন্য মধ্যমপন্থা অবলম্বন করা। নাগরিকদের সংবিধানের মূলনীতির আলোকে শিক্ষিত করে তোলা।
২. শাসক ও শাসিতের সুসম্পর্ক: এরিস্টটলের মতে, শাসক ও শাসিতের সুসম্পর্ক বিপ্লব নিবারণের একটি উৎকৃষ্ট পন্থা। বিশেষ করে শাসকগণ শাসিত-বঞ্চিতদের সাথে উত্তম ব্যবহার করবে। তাতে সাধারণ মানুষের মনের ক্ষোভ দূরীভূত হবে। এজন্য শাসক ও বঞ্চিতদের মধ্যে সুসম্পর্ক অপরিহার্য।
৩. ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ: ক্ষমতা একটিমাত্র কেন্দ্রে থাকলে তা স্বৈরশাসনের পথ করে। জনগণের কাছে ক্ষমতা পৌঁছে দিতে হবে। জনগণের দোরগোড়ায় ক্ষমতা পৌঁছে গেলে বিপ্লব হ্রাস পাবে।
৪. সামাজিক ও অর্থনৈতিক সাম্যঃ এরিস্টটলের মতে, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমতা বিপ্লবের আশঙ্কা হ্রাস করতে পারে বিশেষ করে ধনী ও গরিবদের মধ্যে অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্য হ্রাস করতে হবে। এ ব্যাপারে সরকারের কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত।
৫. আইনের অনুশাসনঃ আইনের অনুশাসন বিপ্লব নিবারণে কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পারে। তাই রাষ্ট্রে আইন অনুসারে শাসন কায়েম করা অপরিহার্য। জনগণকে আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে।
৬. শিক্ষাব্যবস্থার সম্প্রসারণ: বিপ্লব নিবারণের কৌশল হিসেবে এরিস্টটল শিক্ষাব্যবস্থার উপরও গুরুত্বারোপ করেছেন। রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রের অনকূলে শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালনার মাধ্যমে নাগরিক শ্রেণীর মধ্যে রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থার প্রতি শ্রদ্ধাশীল করতে হবে।
৭. ন্যায়ভিত্তিক উপাধি বণ্টন: রাষ্ট্রীয় সম্মান, পদ এবং পুরুষ্কার ন্যায়ের ভিত্তিতে বণ্টন করা হলে বিপ্লবের আশঙ্কা কম থাকে। এসব কাজে জনগণকে সমান এবং প্রাপ্য অধিকার প্রদান করা উচিত। কোনোক্রমেই নাগিরককে তারা প্রাপ্য হতে বঞ্চিত করা উচিত নয়।
৮. শাসকের সতর্কাবস্থা: এরিস্টটলের মতে. বিপ্লব প্রতিরোধের জন্য শাসককে সর্বদা সতর্ক থাকতে হবে। সাধারণ জনগণের উপর যাতে অবিচার করা না হয় এবং গুণী ব্যক্তিরা যাতে তাদের প্রতিভার উপযুক্ত স্বীকৃতি লাভ করতে পারে তা প্রতি শাসক শ্রেণীর সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে।
উপসংহার: পরিশেষে বলা যায় যে, এরিস্টটলের বিপ্লব তত্ত্বটি তার রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মৌলিক অবদানসমূহের মধ্যে অন্যতম। এ তত্ত্বে তিনি বিপ্লবের কারণ ও প্রতিকার ব্যাখ্যায় অত্যন্ত দক্ষ ও নিপুণতার পরিচয় দিয়েছেন। বঞ্চনাবোধ থেকেই যেহেতু বিপ্লবের মূল সুর উত্থিত হয়, সেহেতু বিপ্লব নিবারণের কৌশল হিসেবে তিনি সর্বাগ্রে এ ধরনের মনোবৃত্তির উদয় যাতে হতে না পারে সেদিকে সবিশেষ গুরুত্বরোপ করেছেন। তার মতে, সাম্য, মৈত্রী ও আইনের অনুশাসনই বিপ্লব প্রতিরোধের সর্বাপেক্ষা কার্যকর ওষুধ।
১৯৬৯ গণঅভ্যুত্থান সম্বন্ধে জানতে নিচের লিংকে ক্লিক করুন:
১৯৬৯ সালের গণঅভ্যূত্থান -OnlineRedingRoom (onlinereadingroombd.com)
অনলাইন রিডিং রুম শিক্ষক প্যানেল
 +88 01713 211 910
+88 01713 211 910
